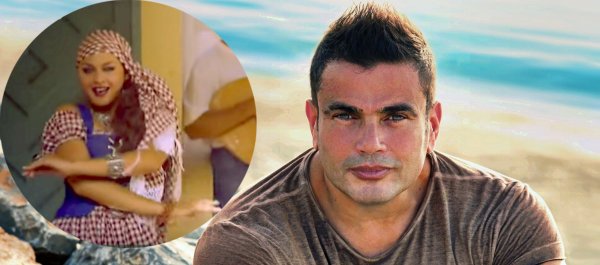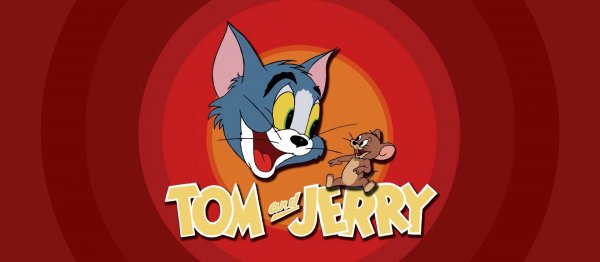তামিলনাড়ুর ভিল্লাপুরাম জেলার উলুন্দুপেত্তাই তালুকের এক শান্ত ও নিরিবিলি গ্রামের নাম কুভাগাম। চেন্নাই শহর থেকে প্রায় একশ নব্বই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই কুভাগাম গ্রামে প্রতি বছর তামিল পঞ্জিকার চিত্তিরাই মাসে অর্থাৎ এপ্রিল মাসের মাঝ বরাবর হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে কুভাগামে। আঠারো দিন ধরে চলে গ্রামের দেবতা কুথান্ডাভার বা আরভানের উদ্দেশ্যে পালিত কুভাগাম উৎসব। এই উৎসবে প্রধানত যোগদান করেন তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা। ভারত তথা দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে এই কুভাগাম উৎসবই হলো তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য অনুষ্ঠিত সবচেয়ে বড় উৎসব।
এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় দেবতা আরাভান বা ইরাবানের মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মবলিদানের এক মহান গাথাকে সম্মান জানিয়ে। মূল সংস্কৃত মহাভারতে এই ঘটনার সেভাবে উল্লেখ না থাকলেও নবম শতকের তামিল সাহিত্যিক পেরুন্তেভানার লেখা মহাভারতের তামিল সংস্করণে এই ঘটনার সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এছাড়া দাক্ষিণাত্যের মানুষের মুখে মুখে আরাভানের বীরত্ব ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কাহিনী প্রচলিত।

এই ইরাবান বা আরাভান ছিলেন মহাভারতের অন্যতম সেরা চরিত্র মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনের পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদীর একান্ত নিভৃত মুহূর্তে বিনা অনুতিতে কক্ষে প্রবেশ করার কারণে অর্জুনকে দ্বাদশ বর্ষের জন্য ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগ করে তীর্থ ভ্রমণে যেতে হয়। ভ্রমণ করতে করতে অর্জুন এসে পৌঁছান ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নাগ রাজ্যে। এখানেই তিনি বিয়ে করেন নাগরাজ কৌরভ্য নাগের কন্যা উলুপীকে। নাগরাজ কন্যা উলুপী ও বীর অর্জুনের পুত্র আরভান একজন নির্ভীক এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হওয়ার পাশাপাশি অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ও নিঃস্বার্থ প্রকৃতির।
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন তাঁর পুত্রদের আহ্বান করলেন পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করার জন্য। আরাভান পিতার ডাকে এসে পৌঁছালেন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে। কৌরব-পাণ্ডব দুই পক্ষেরই যুদ্ধের প্রস্তুতি তুঙ্গে। সময় একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল। যুদ্ধের পূর্বে দেবী আদিপরাশক্তির উপাসনা করে দেবীকে তুষ্ট করে যুদ্ধে জয় নিশ্চিন্ত করার জন্য প্রয়োজন ‘কালাপল্লি’ বা নরবলির। যুদ্ধে যে পক্ষ তার সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধাকে দেবীর কাছে নিবেদন করবে সেই পক্ষের যুদ্ধে জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই যোদ্ধার শরীরে বত্রিশটি দৈব লক্ষণ থাকা অবশ্য প্রয়োজন।
পাণ্ডব পক্ষে কেবলমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন এবং আরাভানের দেহেই সেই দৈব লক্ষণ বর্তমান। আরাভান এবার নিজেই এগিয়ে এলেন। সকলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেবীর উদ্দেশ্যে বলিপ্রদত্ত রূপে ঘোষণা করলেন। কিন্তু তার পূর্বে আরভান তিনটি শর্ত রাখলেন। প্রথমত, তিনি যেন যুদ্ধে বীর যোদ্ধার মতো সম্মানজনক মৃত্যু লাভ করেন, দ্বিতীয়ত, তিনি মৃত্যুর পরেও যেন যুদ্ধ চাক্ষুষ করতে পারেন, এবং তৃতীয়ত, যেহেতু আরাভান অবিবাহিত ছিলেন তাই মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কৌমার্য পরিত্যাগ করতে চান। এই তৃতীয় শর্তের ওপরে ভিত্তি করেই বর্তমানে কুভাগাম উৎসবটি পালন করা হয়।
প্রথম দুটি শর্ত সহজেই মেনে নেওয়া হলো, কিন্তু তৃতীয় শর্ত পালন করতে গিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিল। বিবাহের পরদিনই স্বামীর মৃত্যু নিশ্চিত এমন কাউকে কোনো মেয়েই পতিরূপে বরণ করতে রাজি হলো না। শেষ পর্যন্ত শ্রী কৃষ্ণ তাঁর নারীবেশ মোহিনী রূপ ধারণ করলেন এবং আরভানকে বিয়ে করে রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টম দিনে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে অলম্বুস নামক এক রাক্ষসের হাতে আরাভানের মৃত্যু হয়। আরাভানের শোকে মোহিনীরূপী শ্রী কৃষ্ণ তাঁর বিবাহের চিহ্ন মুছে ফেলে আকুল হয়ে ক্রন্দন করতে করতে বিধবার পোশাক পরিধান করেন। এরপরে আরাভানের কর্তিত মস্তক একটি বড় বর্শার ফলায় গেঁথে যুদ্ধক্ষেত্রে রাখা হয় যাতে তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে সমস্ত যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে পারেন। এই কারণেই আরাভানের মন্দিরে কেবলমাত্র তাঁর কর্তিত মস্তকই পূজিত হয়।

প্রতি বছর তামিল চিত্তারাই মাসে আরাভানের আত্মবলিদান, শ্রী কৃষ্ণের মোহিনী বেশে তাঁর মৃত্যুতে ক্রন্দন ও বৈধব্য পালন এই পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুথান্ডাভার বা আরাভানের উপাসনা করা হয় এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের মহিলারা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। কারন তাঁরা মনে করেন হিজড়া জনগোষ্ঠীর আদি দেবতা আরাভান এবং তাঁরা মোহিনী ও আরাভানের সন্তান। তাই তাঁরা নিজেদের ‘আরাভানিয়ান’ বলেও পরিচয় দেন।
কুভগাম গ্রামের আরাভানের মন্দির ঘিরে আঠারো দিনব্যাপী এক বর্ণাঢ্য উৎসবের আয়োজন করা হয়। শুধুমাত্র ভারত নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের মানুষেরা এসে কুভগামে এসে জড়ো হন। প্রতিদিন স্থানীয় নাচ, গান ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বর্তমানে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নানা ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালায়। এছাড়া একটি বাৎসরিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ‘মিস কুভাগম’ আয়োজন করা হয় যেখানে শুধুমাত্র বৃহন্নলা নারীরা অংশগ্রহণ করেন। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য আয়োজিত এই অভিনব উদ্যোগ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রথম ষোল দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরে সতেরতম দিনে শুরু হয় আসল উৎসব।

এই দিন হিজড়া সম্প্রদায়ের মহিলারা নববধূর মতো শৃঙ্গার করেন। বিবাহের চিহ্নস্বরূপ মাথায় ‘গজরা’ বা ফুলের মালা জড়ান এবং গলায় ‘থালি ‘ বা মঙ্গলসূত্র পরেন, হাতে পরেন কাচের চুড়ি এবং সিঁথিতে সিঁদুর লাগান। এভাবে তাঁরা ভগবান আরাভানের নবপরিণীতা বধূ হিসেবে নিজেদের দেবতার চরণে সমর্পন করেন। এদিন রাতভর স্থানীয় ভাষায় নাচ, গান করে বিয়ের অনুষ্ঠানকে উপভোগ করা হয়। পরদিন মন্দির থেকে আরাভানের প্রতীক কাষ্ঠনির্মিত মস্তক নিয়ে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। লাখ লাখ মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন। আরাভানকে অনেক ফুলের মালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর যে মহিলারা আরাভানের নববধূ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তারা শোকপালন শুরু করেন। মন্দিরের পুরোহিত তাদের গলায় বাধা মঙ্গলসূত্র ছিড়ে দেন এবং হাতের চুড়ি ভেঙে দিয়ে সিঁদুর মুছে দেন। তারপরে বুক চাপড়ে উচ্চস্বরে বিলাপ করতে করতে আরাভানের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে থাকেন।
এ সময় আরাভানের মৃত্যুর প্রতীকস্বরূপ তাঁর গলায় ঝুলতে থাকা ফুলের মালাও টেনে টেনে ছিড়ে ফেলা হয়। এরপরে রঙিন শাড়ি ছেড়ে স্নান করে বৈধব্যের শুভ্র বেশ ধারণ করেন। এভাবেই অষ্টাদশ দিবসব্যাপী উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই বৈধব্য সাজ তারা মাসখানেক পালন করেন। তারপর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান।

যুগ যুগ ধরে হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা ভারতীয় সমাজে অবহেলিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত হয়ে চলেছে। ট্রেনে, বাসে রাস্তায় বৃহন্নলাদের দেখে বিরক্তিতে মুখ বেঁকে যায় অনেকেরই। দীর্ঘ কয়েক দশকের কঠিন লড়াই শেষে তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি পেলেও সমাজের চোখে আজও তারা ব্রাত্য। হিন্দু ধর্মে একসময় যাঁদের অর্ধনারীশ্বর বা ভগবান শিব এবং আদি শক্তি মহামায়ার এক সম্মিলিত রূপ হিসেবে পূজা করা হত, সম্মান করা হত স্বয়ং শিব ও শক্তির আশীর্বাদধন্য কিন্নর সম্প্রদায় হিসেবে, সেই মানুষগুলো আজ সমাজের এককোণে অবহেলায় পড়ে থাকে।
কুভাগম উৎসব যেন এই সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে এই প্রান্তিক মানুষগুলোরও নিজেদের মতো করে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। উৎসবের এই দিনগুলোতে তারা নিজেদের মতো করে অনেক আনন্দ করে। নাচ, গান, হইহুল্লোড় করে তাদের অপমানজনক জীবনের গ্লানি কিছুটা হলেও ভোলার চেষ্টা করে।

তারা নিজেদের স্বয়ং শ্রী কৃষ্ণের মোহিনী অবতারের অংশ বলে গণ্য করেন এবং দেবতা আরাভানকে বিয়ে করে সেই স্বীকৃতি লাভেরই চেষ্টা করেন। এই উৎসবকে ঘিরে আঠারো দিন ধরে যেসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তার মধ্যে সাম্প্রতিকতম সংযোজন হলো শুধুমাত্র তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আয়োজন।২০০০ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় এবং প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এভাবেই বোধহয় সমাজের পদদলিত এই মানুষগুলো একদিনের জন্য হলেও নিজেদের দৈনন্দিন সমস্ত দুঃখ, সমস্ত অপমান ভুলে জীবনের আনন্দের স্বাদ উপভোগ করেন; একরাতের জন্য হলেও বিয়ের সুখ অনুভব করতে পারেন যে সুখ থেকে তারা চিরকালই বঞ্চিত।
এই কুভাগাম উৎসব যেন এই গতানুগতিক সমাজকে হিজড়াদের এক অন্যরকম দৃষ্টিতে দেখার চোখ খুলে দেয়। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদেরকে তাদের ব্যক্তিগত যৌন পরিচয় বাদ দিয়ে রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে স্বীকার করা এবং সর্বোপরি তাদের মানবিক অনুভূতিগুলোকে সম্মান জানানো যে প্রয়োজন, তা যেন সমাজের জীর্ণ ধ্যানধারণার গালে এক সপাটে থাপ্পর মেরে বুঝিয়ে দেয়।