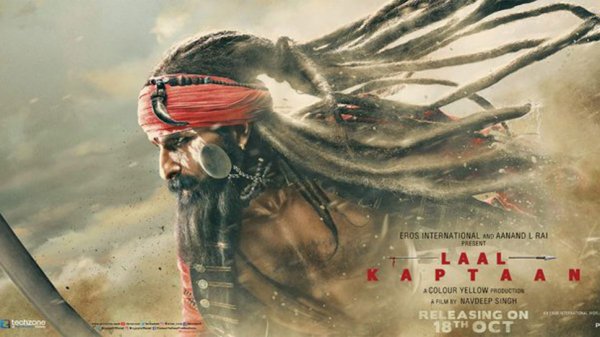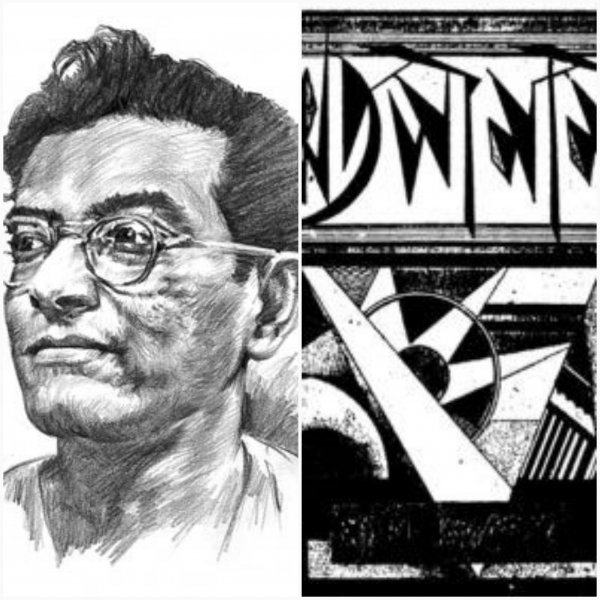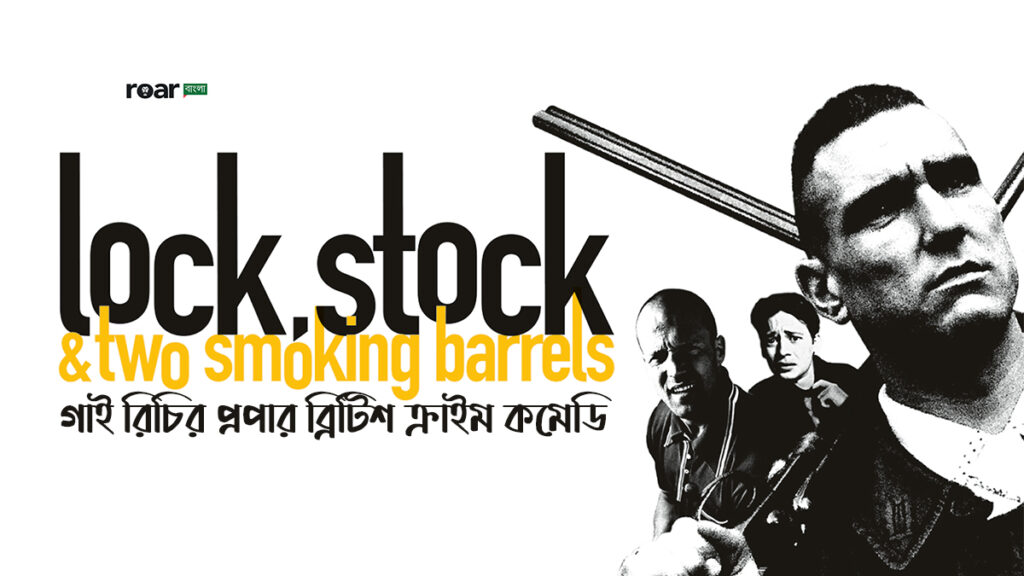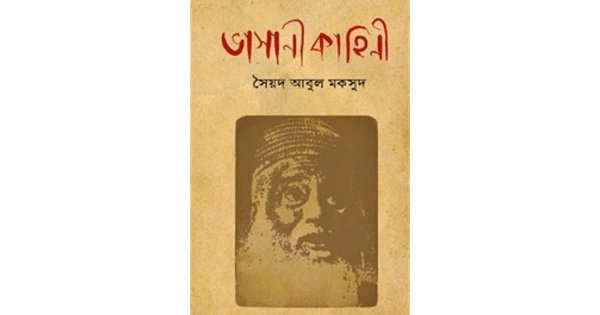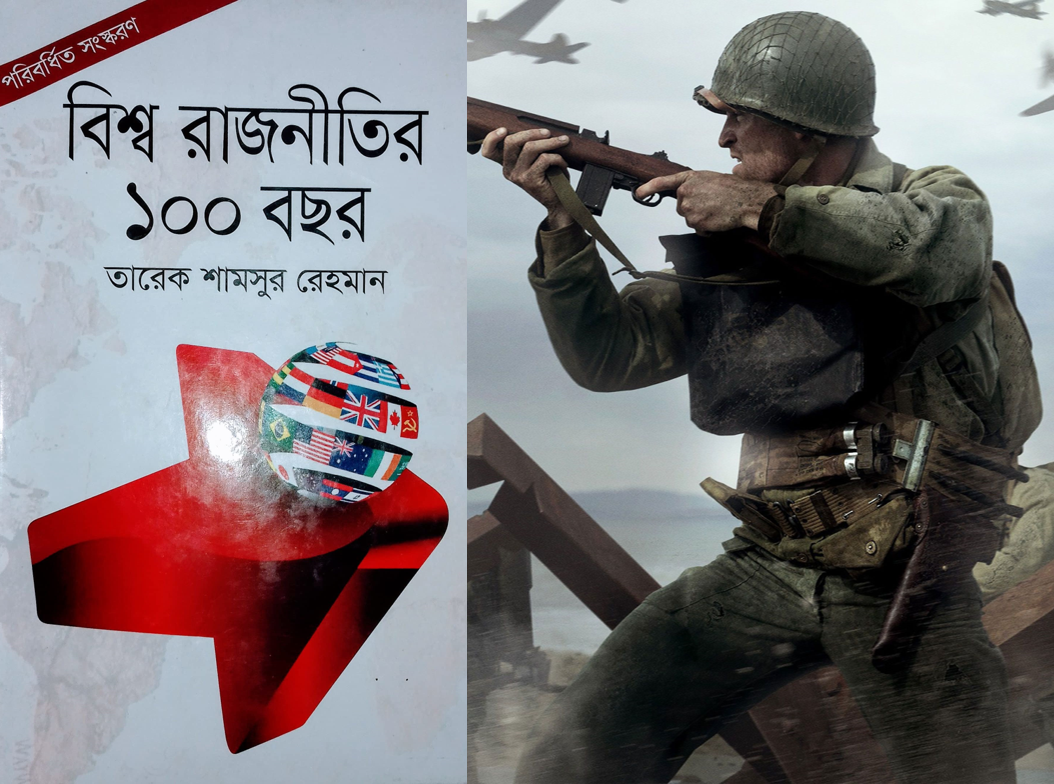
বইয়ের সংস্পর্শে এসেও বই ভালো লাগেনি, বোধ করি এমন মানুষের সংখ্যাটা খুব কম। তবে পছন্দের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। কারো গল্প ভালো লাগে, কারো কবিতা। কারো হয়তো ভ্রমণ কাহিনী, কারো সভ্যতা, আবার কেউ কেউ হয়তো ভালোবাসেন যুদ্ধ-সংঘাত বা রাজনৈতিক ইতিহাস। প্রত্যেক পাঠকই তার পছন্দের বিষয় নিয়ে লেখা বই পড়তে ভালোবাসেন। ‘বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর‘ বইটি তাদের জন্য, যারা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ইতিহাস ও সমসাময়িক ভূ-রাজনীতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।
বর্তমান সময়ে আলোচিত বিশ্ব রাজনীতির সব ঘটনাই গত ১০০ বছর কিংবা তারও অনেক আগের কোনো না কোনো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বা সংঘাতের সাথে সম্পর্কিত। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতি বুঝতে হলে এর অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা থাকাটা জরুরি।

ড. তারেক শামসুর রেহমান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান। আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে তার বিশ্লেষণ অসাধারণ। তিনি বিশ্ব রাজনীতির কূটকৌশল নিয়ে অসংখ্য বই রচনা করেছেন। ‘বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর’ বইটিতে তিনি গত ১০০ বছরে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ চমৎকার তথ্যবহুলভাবে বর্ণনা করেছেন। বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে এমন ধারাবাহিক বর্ণনার বই খুব একটা পাওয়া যায় না। তাই বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে আগ্রহী পাঠকদের কাছে বইটি বেশ জনপ্রিয়।
বইটি পড়ে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা যাবে
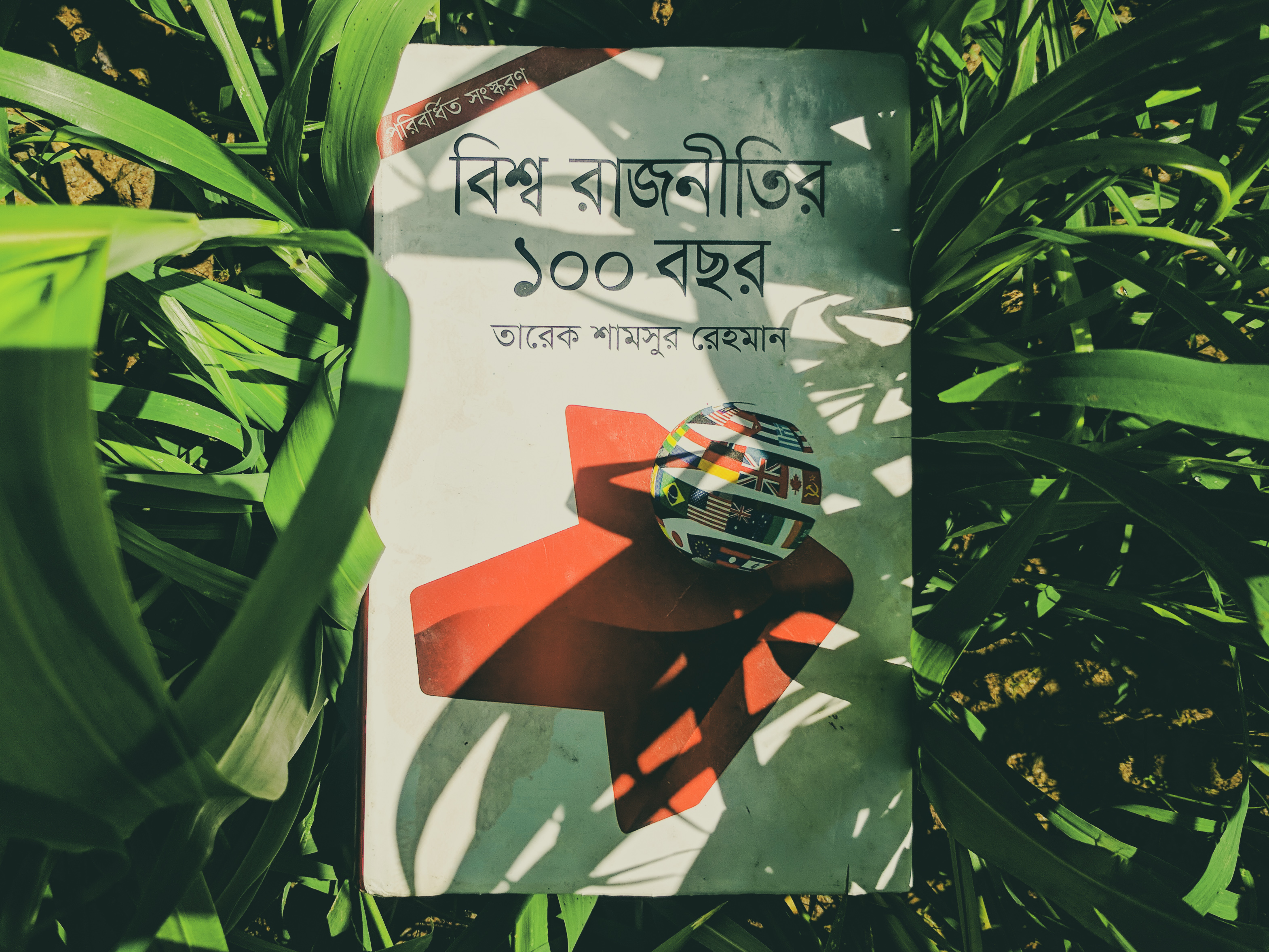
১
গত শতাব্দীর শুরুতেই বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর একটি হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)।
কেন্দ্রীয় শক্তিজোট (জার্মানি, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক) ও মিত্র শক্তির (রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, সার্বিয়া, বেলজিয়াম) নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো পৃথিবী এত বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়ায়। একই সময়ে রুশ বিপ্লব চূড়ান্ত সফলতা অর্জনের মাধ্যমে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রুশ বিপ্লব ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়। প্রত্যেকটি দেশ যুদ্ধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে। এবং ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলা করতে একটি আন্তর্জাতিক ঐক্যের প্রচেষ্টা চালায়। ফলে জাতিপুঞ্জ বা লিগ অব নেশন্স-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা আত্মপ্রকাশ করেছিল। এদিকে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে তাদের আর্থসামাজিক জীবনে নানা ইতিবাচক-নেতিবাচক পরিবর্তন আসে।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের মাধ্যমে সাময়িক শান্তি ফিরলেও অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবী আরো একটি ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পতনের পর দীর্ঘদিন সেখানে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব থাকলেও হিটলারের উত্থানের পর জার্মানি আবার ঘুরে দাঁড়ায়। হিটলারের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, এক তরফা ভার্সাই সন্ধি ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জার্মানির প্রতি বৈষম্যমূলক নীতিগুলোই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে। আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিপুঞ্জ এই সংকট মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। কারণ বৈশ্বিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সংস্থাটির জন্ম হলেও তৎকালে যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রের অসহযোগিতার কারণে সংস্থাটি অকার্যকর হয়ে পড়েছিল।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও জার্মানি পরাজিত হয়। যুদ্ধে জার্মানি ও অক্ষশক্তি পরাজিত হলেও মিত্রশক্তির প্রধান দুই শক্তিশালী দেশ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স অর্থনৈতিকভাবে একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বিশ্বে নতুন পরাশক্তি হিসেবে রাশিয়া ও আমেরিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ইউরোপে ইংল্যান্ড-ফ্রান্সের দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগায় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দেশ রাশিয়া (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরাজিত এলাকাগুলোর উপর মিত্রশক্তির দেশগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। বিশেষ করে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়। মূলত সে সময়টাতেই আমেরিকা রাশিয়ার অঘোষিত প্রতিপক্ষে রূপ নেয়।
২
অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে পৃথিবী দুটি ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ইতোপূর্বের সকল যুদ্ধের আতঙ্ককে ছাপিয়ে যায়। কারণ এই যুদ্ধে প্রথমবারের মতো বিশ্ববাসী পারমাণবিক বোমার ভয়াবহতা দেখতে পায়। তবে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও নতুন বিশ্বের দুই পরাশক্তির উত্থান যেন আরো একটি যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করে। রাশিয়া ও আমেরিকা একে অপরের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে ভয়াবহ রকমের শক্তিশালীভাবে গড়ে তুলতে থাকে। তৎকালে দুই দেশের এই প্রতিযোগিতায় তৈরি হওয়া যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিস্থিতি ইতিহাসে স্নায়ুযুদ্ধ নামে পরিচিত।
পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর উপর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ ও বিপরীতে আমেরিকার রাশিয়া বিরোধী জোট গঠন যেন সারা বিশ্বকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দিচ্ছিল। এই ভাগাভাগির রাজনীতির মূলে ছিল ইউরোপের দেশগুলোকে নিয়ে আমেরিকার সামরিক জোট ন্যাটোসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক জোট গঠন। এরূপ পরিস্থিতিতে জাতিপুঞ্জের মতোই জাতিসংঘও অনেকটা নিষ্ক্রিয় ছিল। আমেরিকা-রাশিয়ার পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দ্বন্দ্বের ডামাডোল বিশ্বে এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে ভিয়েতনাম থেকে কোরিয়া পর্যন্ত এর উত্তাপ ছড়িয়ে যায়।
এরূপ পরিস্থিতিতে আরো একটি আন্দোলনের সূচনা হয়, যা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মূলত পরাশক্তিধর রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব থেকে যেন দুর্বল দেশগুলো দূরে থাকতে পারে।
৩
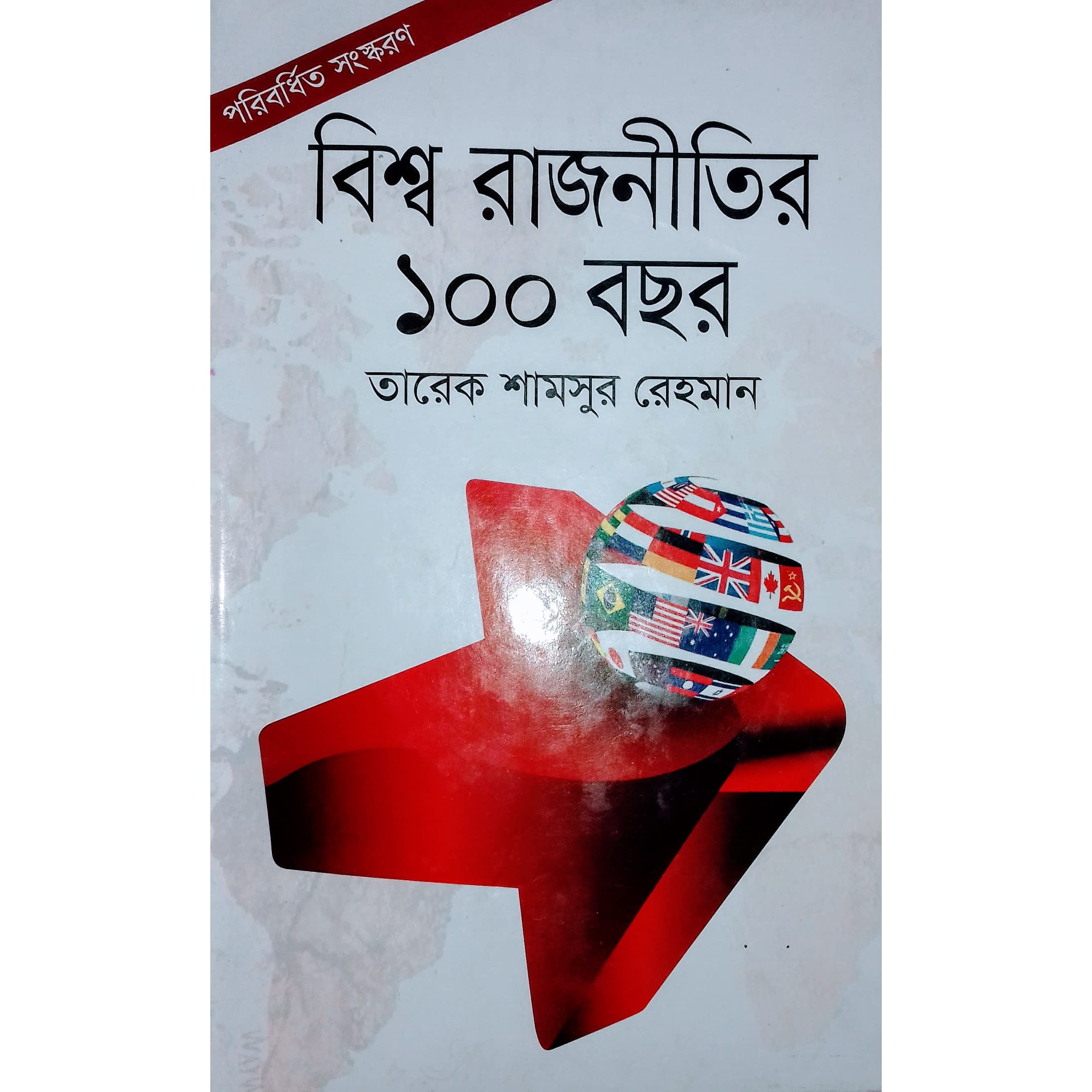
‘বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর’ বইটিতে মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই বইটিতে গত শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের কারণ ও এর ফলে বদলে যাওয়া রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের তাথ্যিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। কীভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু হলো, আফগানিস্তানে রাশিয়া-আমেরিকার দখলদারিত্ব, দুই কোরিয়ার সমস্যা, জার্মানির বিভক্তি ইত্যাদি আছে। বাদ যায়নি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ, উপসাগরীয় যুদ্ধ, কিউবা সংকটসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও।
এছাড়াও আমেরিকা-রাশিয়া দ্বন্দ্বের আড়ালে নীরবে চীনের উত্থান। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরবর্তীতে সময়ে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে শক্তিশালী হওয়া চীনের অপার সম্ভাবনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানা যাবে বইটিতে।
যদিও বইটিতে অত্যধিক তথ্যের সমাবেশের কারণে পাঠক অথৈ সাগরে পড়ার মতো বোধ করতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার এই বইটিতে গত ১০০ বছরের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও হয়তো অনেক বই পাওয়া যাবে, যেগুলোতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু এই বইটিতে স্বল্প পরিসরে গত শতাব্দীর প্রায় সব রাজনৈতিক ঘটনার মৌলিক বিষয়াদি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি বুঝতে হলে, গত ১০০ বছরের রাজনীতির যে বিষয়গুলো সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকা প্রয়োজন, প্রায় সব কিছুই পাওয়া যাবে বইটিতে।
অনলাইনে বইটি সংগ্রহ করতে ক্লিক করতে পারেন নিচের লিঙ্কে: