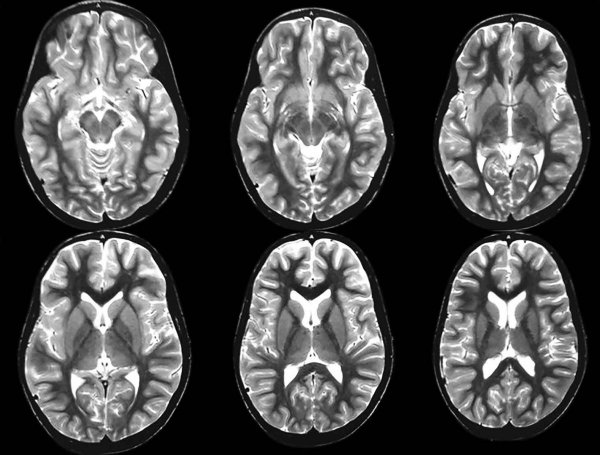করোনা মহামারির মধ্য দিয়ে টিকার ইতিহাসে রচিত হয়েছে নতুন এক অধ্যায়। জার্মান বায়োটেক কোম্পানি বায়োএনটেক পৃথিবীবাসীর কাছে সর্বপ্রথম কোনো mRNA ভ্যাক্সিন উপস্থিত করল। বায়োএনটেকের সহপ্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আছেন উর শাহিন ও ওজলেম টুরেজি। তাদের ও তাদের দলের অসামান্য কর্মদক্ষতায় ও বিচক্ষণতায় প্রতিষ্ঠানটি এত অসাধারণ প্রযুক্তির এই ভ্যাক্সিন আমাদের কাছে দিতে পেরেছেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ফাইজারের সাথে যৌথ উদ্যোগে বায়োএনটেক প্রস্তুত করেছে তাদের ভ্যাক্সিন। বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের কাছে তারা এই বিশাল কর্মযজ্ঞের খুঁটিনাটি তুলে ধরেছে। পাঠকদের জন্য থাকছে টাইম ম্যাগাজিনের সেই প্রতিবেদনের ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ।

গেল বছরের জানুয়ারির শেষ নাগাদ শাহিন যখন উহানের ব্যপারে গবেষণা করছিলেন তখনই বুঝতে পারেন, এই মহামারি খুব শীঘ্রই শেষ হওয়ার নয়। তার ধারণায় এতটুকু ছিল যে, মহামারিটি কোনো আঞ্চলিক দুর্ঘটনা নয় বরং খুব সম্ভবত ইতোমধ্যে ভাইরাসটি পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি জানতেন যে, সংক্রমণ রোধে এক মুহূর্ত সময়ও নেই অপচয় করার মতো। তবে মেইনজ ভিত্তিক বায়োএনটেক মূলত একটি ক্যান্সার ভ্যাক্সিন তৈরিকারী প্রতিষ্ঠান। এটি প্রায় এক দশকের প্রচেষ্টায় ক্যান্সারের mRNA ভ্যাক্সিনের একটি ট্রায়ালের (স্যাম্পল সাইজ-৪০০ জন) সন্তোষজনক ফলাফল লাভ করেছে। সে সময় তারা মূলত ফ্লুয়ের মতো সংক্রামক ব্যাধিসমূহের জন্য একটি mRNA ভ্যাক্সিন তৈরির চিন্তাভাবনা করছিলেন।

উর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন পদে আসীন ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে। প্রাথমিকভাবে ৪০ জনের উপস্থিতিতে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে তারা এই প্রজেক্টটির নামকরণ করবেন- ‘প্রজেক্ট লাইটস্পিড’। ৪০ জনের সেই দল কিছুদিনের মাঝেই ২০০ জনের দক্ষ একটি জনবলে পরিণত হয় এবং আক্ষরিক অর্থেই দিন রাত কাজ করা শুরু করে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে mRNA ভ্যাক্সিন প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে। টানা কয়েক সপ্তাহের মাঝেই তারা ২০টি ক্যান্ডিডেট ভ্যাক্সিন তৈরি করতে সক্ষম হন যার মাঝে ৪টি অভূতপূর্ব কার্যকারিতা প্রদর্শন করে। বায়োএনটেকের mRNA বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং বিভাগের সহ সভাপতি অ্যান্ড্রিস কুন সবাইকে ডেকে বলেন,
এতদিন যার যা দায়িত্ব ছিল সবকিছু আমাদের সত্যিই ভুলে যেতে হবে। এই মুহূর্ত থেকে আমাদের একমাত্র চিন্তাভাবনা করোনা মহামারিকে রুখে দেওয়ার জন্য একটি কার্যকরী mRNA ভ্যাক্সিন তৈরি করা।
শীঘ্রই তারা সার্স ও মার্স ভাইরাস দুটির উপর বিস্তর গবেষণা শেষে সার্স কোভ-২ এর বিরুদ্ধে একটি কার্যকরী ভ্যাক্সিন প্রস্তুতের লক্ষ্যে ৫০,০০০ ধাপবিশিষ্ট একটি পদ্ধতি দাঁড় করিয়ে ফেলেন।

পুরো প্রক্রিয়াটির শুরু হয় স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি ৫০ লিটার ধারণক্ষমতার একটি ট্যাংক দিয়ে। ট্যাংকটি দেখতে অনেকটা বিয়ারের কেগের মতো। এই ট্যাংকের ভেতরে থাকে mRNA-র টুকরো যেগুলো সার্স কোভ-২ ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনকে কোড করতে সক্ষম। ভ্যাক্সিন প্রস্তুতকরণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় একটি হারমেটিক্যালি সিল্ড (সম্পূর্ণভাবে বায়ুনিরোধী) সিস্টেমের মাঝে। প্রতিটি ধাপের শেষে উৎপন্ন দ্রব্যকে পরের ধাপে নিয়ে যাওয়ার জন্য রয়েছে প্লাস্টিক টিউব নির্মিত একটি নেটওয়ার্ক।

সর্বোচ্চ পর্যায়ের জৈব সুরক্ষা রক্ষার্থে এবং যেকোনো ধরনের অবাঞ্ছিত সংক্রমণ রোধকল্পে প্রতিষ্ঠানটির টেকনিশিয়ানরা নিয়মিত বিরতিতে ম্যানুফ্যাকচারিং রুমসমূহের এয়ার কোয়ালিটি (বায়ুর বিশুদ্ধতা) নির্ণয় করে থাকেন। এতে করে সেখানকার বায়ুতে যেকোনো ধরনের অণুজীব উপস্থিত থাকলে সেটি তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে যাবে। এছাড়াও ভ্যাক্সিন নিয়ে যারা সরাসরি কাজ করে থাকেন তারাও নির্দিষ্ট সময় পরপর একধরনের বিশেষ অ্যাগারে গ্লাভস সমেত আঙ্গুল প্রবেশ করান। এই অ্যাগারটির বিশেষত্ব হচ্ছে এটি যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাকটেরিয়াকে কালচার করতে পারবে। অর্থাৎ, সেই অ্যাগারে যদি কোনো ব্যাকটেরিয়ার নামমাত্র উপস্থিতি পাওয়া যায় তাহলে চটজলদি ব্যবস্থা নেওয়া হয় যাতে সেটি কোনোভাবেই ভ্যাক্সিন পর্যন্ত যেতে না পারে।

জৈব অণু হিসেবে mRNA অনেক অস্থিতিশীল। এটি তার মূল রূপে (raw form) মানবদেহে টিকে থাকতে পারে না। একে সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রেসারাইজড ইথানল ব্যবহার করে mRNA-এর চারপাশে লিপিড (স্নেহ জাতীয় পদার্থ) বাবল জুড়ে দেওয়া হয়। এই অংশটুকু সম্পন্ন হয় একই ধরনের ৬টি ৫০ লিটার ধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট ট্যাংকের যেকোনো একটিতে। প্রতিটি ট্যাংক একেকটি আলাদা সীলকৃত রুমে অবস্থান করে। এই ৬টি রুমে শুধু অনুমোদিত ব্যক্তিরাই প্রবেশাধিকার রাখেন।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইথানল অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ বিধায় এসব রুমে চলাচল করার সময় স্ট্যাটিক ফ্রি জুতো পরিধান করা আবশ্যক। অর্থাৎ, সাধারণ জুতো পরে এসব রুমে হরদম যাতায়াত করলে রুমের মেঝের সাথে জুতোর সামান্য ঘর্ষণেও ইথানলের উপস্থিতিতে অনেক বড় বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। সেই ন্যুনতম বিপদের ঝুঁকিকেও নাকচ করে দেওয়ার জন্যই এই বিশেষ জুতো পরার বিধান। এই ৬টি ট্যাংকের নামকরণ করা হয়েছে ভ্যাক্সিন প্রস্তুতের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ৫ জনের নামানুসারে। ষষ্ঠ ট্যাংকটির নামকরণ করা হয়েছে মার্গারেটের নামে যিনি যুক্তরাজ্যের প্রথম ফাইজার-বায়োএনটেকের ভ্যাক্সিন গ্রহীতা ছিলেন।
mRNA-কে ঘিরে থাকা লিপিড বাবল নির্মাণের মাধ্যমে ইথানলের দায়িত্ব সম্পন্ন হয়। এরপর একে একাধিকবার ফিল্টার করা শেষে একটি দুধ সদৃশ তরল পাওয়া যায়। এই দ্রবণটিকে ১০ লিটারের প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে ফিল-অ্যান্ড-ফিনিশ দশায় স্থানান্তর করে দেওয়া হয়। এই ধাপে চলে বিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া এবং এরপর স্টেরাইল (জীবাণুমুক্ত) ভায়ালে ভ্যাক্সিন প্রবেশ করানো হয়। একেকটি ভায়ালে থাকে ৬টি ডোজের সমপরিমাণ ভ্যাক্সিন, যেগুলো বিশ্বের নানা হাসপাতাল আর ক্লিনিকে পৌঁছে যায়।

বর্তমানে প্রতি ৩-৭ দিনে বায়োএনটেক তাদের ভ্যাক্সিনের ৮ মিলিয়ন ডোজ প্রস্তুত করে যাচ্ছে। পূর্ণ কর্মদক্ষতায় কাজ করলে প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর ১ বিলিয়ন ডোজ প্রস্তুত করতে পারবে বলে বিশ্বাসী। এবং ২০২১ সালের শেষ নাগাদ সর্বমোট ২.৫ বিলিয়ন ডোজ তারা পুরো পৃথিবীর কাছে তুলে দিতে পারবে বলে আশা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ফাইজারের সার্বিক সহযোগিয়তায় তারা এই কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছে মারবার্গ সাইটে। নোভার্টিস থেকে বায়োএনটেক এই জায়গাটুকু কিছুদিন আগে কিনে নেয়। নোভার্টিসের অধিকাংশ ল্যাব টেকনিশিয়ানরা পরবর্তীতে বায়োএনটেকে যোগদান করে।
এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। নোভার্টিস থেকে যেসব ল্যাব টেকনিশিয়ান বায়োএনটেকে যোগদান করেছেন তারা সবাই নোভার্টিসের ল্যাব কোটই পরিধান করেন। কেন? ভ্যাক্সিন প্রস্তুতকরণে পুরো দলটি এতটা গভীরভাবে সংকল্পবদ্ধ যে তারা নতুন করে বায়োএনটেকের লোগো সম্বলিত ল্যাব কোট অর্ডার করে সময় নষ্ট করতে চান না। তাদের বিবেচনায় শুধু এটুকু বর্তমান যে, ল্যাব কোটটি কাজের জন্য উপযুক্ত কি না? এতে কোন প্রতিষ্ঠানের লোগো আছে সেটি নিয়ে তারা কালক্ষেপণ করতে রাজি না কোনোভাবেই।
বায়োএনটেকের গল্পটা এখানেই শেষ নয়। গবেষক দম্পতি এবং পুরো দল ইতোমধ্যেই করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধেও একটি ভ্যাক্সিন তৈরি করেছেন এবং অপেক্ষায় আছেন এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করার। নিরন্তর শুভ কামনা তাদের জন্য।