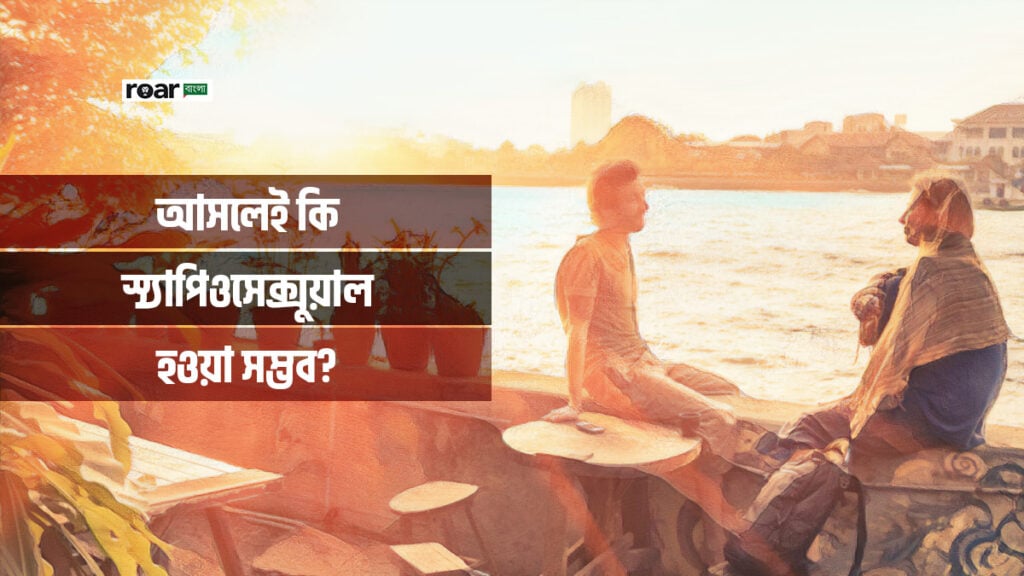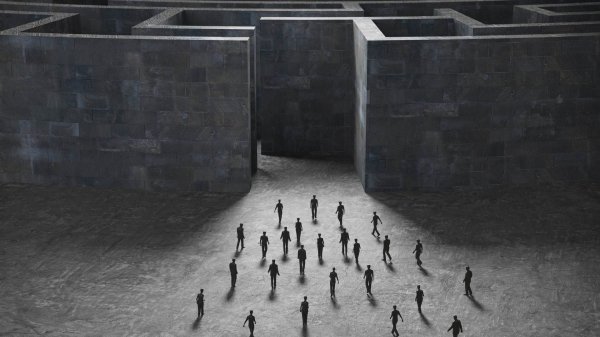(পর্ব ৯ এর পর থেকে)
অ্যাপোলো-১৩ এর সাথে জড়িতদের কাছে দুর্ঘটনার পরের সময়গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক, কমান্ড মডিউল নিষ্ক্রিয় করার আগে পর্যন্ত সময়টা। দুই, নভোচারীদের চাঁদকে ঘিরে আসার বিশ ঘণ্টা সময়টা। তিন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসার সময়টা। এর মাঝে দ্বিতীয় ধাপের সময়টা ছিল সবচেয়ে অনিশ্চয়তায় মোড়ানো। তখন ফ্লাইট কন্ট্রোলারদের বিস্তৃত পরিসরে চিন্তা করতে হচ্ছিল।
তৃতীয় তলায় স্টাফ সাপোর্ট রুমে স্পেসক্রাফট আর কমিউনিকেশন লুপের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য টেলিভিশন স্ক্রিন আর হেডসেটের ব্যবস্থা ছিল। উপরের তলায় ব্ল্যাক টিম তখন খুবই ব্যস্ত থাকায় ক্রাঞ্জ ও তার টিমের সদস্যরা বৃহৎ পরিসরে পরিকল্পনা করতে থাকেন। নভোচারীরা যারা মনে করতেন তারাই স্পেসক্রাফট পরিচালনা করেন, তারা অ্যাপোলো-১৩ নিয়ে বলেন এটা ছিল পুরোটাই ‘গ্রাউন্ড শো’।
ফ্লাইট কন্ট্রোলাররা একে বলে থাকেন ‘রেট্রো মিশন’। কারণ রেট্রোফায়ার অফিসার আর তার সহযোগী ফ্লাইট ডিনামিকস অফিসার ছিলেন স্পেসক্রাফট পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বে। রেট্রো ও ফিডো অফিসাররা ট্রেঞ্চে এত কাছাকাছি কাজ করতেন যে, তাদের আলাদা করা সম্ভব হতো না। সে মুহূর্তে অ্যাপোলো-১৩ স্পেসক্রাফটের গতির দিক এমনভাবে ছিল যে, এটা চাঁদকে ঘিরে পৃথিবীর দিকে আসতে চার দিনের বেশি সময় লাগবে। কিন্তু এর অবস্থান এমনভাবে ছিল যে, পৃথিবীর চল্লিশ হাজার মাইল দূরবর্তী স্থান দিয়ে অতিক্রম করে যাবে।

প্রধান রেট্রো অফিসার দিয়েত্রিখ কিছু বিকল্প রাস্তা খোঁজা শুরু করলেন গতিপথ সংশোধন করার জন্য। প্রথম উপায় ছিল মডিউলের রকেটের জ্বালানি অল্প পরিমাণ চালু করা। কিন্তু টেলমুর পক্ষ থেকে তখুনি এটা বাতিল করে দেওয়া হয়। টেলমু প্রধান উইলিয়াম পিটার কেবল কথপোকথনে যোগ দেন। তিনি জানান এতে স্পেসক্রাফটের গতি খুব একটা বাড়বে না। বরঞ্চ লুনার মডিউলে থাকা চার দিনের মজুদ ক্ষতিগ্রস্ত করবে। যদিও স্পেসক্রাফট অ্যানালাইসিস টিমের পক্ষ থেকে জানানো হয় লুনার মডিউলে চার দিনের বেশি সময়েরও প্রয়োজনীয় অক্সিজেন মজুদ আছে। কিন্তু বিদ্যুৎ আর পানির সরবরাহ নিয়ে তখনো সংশয় ছিল।
দিয়েত্রিখ তখন আরেকটি প্রস্তাবনা নিয়ে আসেন, যদিও এটা নতুন কিছু ছিল না। তিনি বলেন স্পেসক্রাফটটা চাঁদকে ঘিরে আসা পর্যন্ত প্রায় আঠারো ঘণ্টা সময় অপেক্ষা করতে। এরপর রকেটকে পুরোদমে চালু করতে। এই প্রস্তাব টেলমুকে আকর্ষিত করে। কিন্তু প্রধান কন্ট্রোল অফিসার হেরল্ড লডেন এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

প্রত্যেক ফ্লাইট কন্ট্রোলারই স্পেসক্রাফট বা নভোচারীদের রক্ষার জন্য কাজ করলেও তাদের মধ্যে আলোচনাগুলো পরস্পরবিরোধী মনে হচ্ছিল। ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। লুনার মডিউলের দিকনির্দেশনা ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কন্ট্রোল অফিসাররা জানান দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী রকেটকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করলে জ্বালানির পরিমাণ একেবারে শেষ হয়ে যাবে। এতে যাত্রা মাঝ পথে সংশোধনের দরকার পড়লে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে।
দিয়েত্রিখের তৃতীয় প্রস্তাবনা ছিল প্রথম দুটি প্রস্তাবের সম্মিলিত রূপ। তিনি পরামর্শ দেন পরবর্তী ঘণ্টায় ক্ষুদ্র সময়ের জন্য রকেটের জ্বালানি পোড়ানো। এতে স্পেসক্রাফটের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে পৃথিবীর দিকে মুক্তভাবে আসবে। যদিও এটা সুনির্দিষ্টভাবে অবতরণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এরপর চাঁদকে প্রদক্ষিণ করা শেষে দ্বিতীয়বারের মতো রকেটের জ্বালানি পোড়াতে বলেন। এতে মহাকাশযানের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হবে এবং গতিও বাড়বে। কয়েকজন ফ্লাইট কন্ট্রোলার এই প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করেন। কারণ এই প্রক্রিয়াটা ছিল অনেক জটিল। দুই বার রকেটের জ্বালানি পোড়ানোর বিষয়টা কেউই পছন্দ করেন না, যেখানে একবারই যথেষ্ট ছিল।

উদাহরণস্বরূপ টেলমুর কথা বলা যায়। তারা বলেন জ্বালানি দুই বার পোড়ালে বিদ্যুৎ আর পানির পরিমাণ দ্বিগুণ লাগবে একবার পোড়ানোর তুলনায়। প্রতিবার জ্বালানি পোড়ানোর সময় যন্ত্রপাতিগুলোকে চালু করতে হবে ও ঠাণ্ডাও রাখতে হবে। এদিক বিদ্যুৎ আর পানির পরিমাণ নিশ্চিতভাবেই ছিল অপর্যাপ্ত। দিয়েত্রিখ তৃতীয় প্রস্তাবটাই পছন্দ করেন। কারণ এটাই ছিল সবচেয়ে সহজ উপায়। কারণ এতে চাঁদকে ঘিরে আসার পর রকেট চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা থাকে। এরপর পরিস্থিতি বিবেচনা করে রকেটকে দ্রুত গতিতে কিংবা ধীর গতিতে পরিচালনা করা যেতে পারে।
ক্রাঞ্জ অনুমতি দেওয়ায় এই পরিকল্পনাই গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার একটা দিক সবাইকেই স্বস্তি এনে দেয়। এতে অন্তত পৃথিবীর দিকে স্পেসক্রাফট ফিরিয়ে আনার জন্য একটা ধাপ অতিক্রম করা হচ্ছে। লাভেল বলেছিলেন, সে মুহূর্তে তার মূল উদ্বেগ ছিল অন্তত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আসা। কারণ তার কাছে মনে হয়েছিল মহাকাশযান নিয়ে পৃথিবীতে না আসতে পারার চেয়ে পৃথিবীতে উল্কাপিণ্ডের মতো জ্বলন্ত অবস্থায় পতিত হওয়া ভালো। কন্ট্রোল রুমে থাকা দিয়েত্রিখ ও অন্যান্য ফ্লাইট কন্ট্রোলাররা চাচ্ছিলেন অবিলম্বে প্রথমবারের মতো জ্বালানি পোড়ানোর কাজ সেরে ফেলতে। কিন্তু নভোচারীরা একটু সময় চান। এটা এক ঘণ্টার কিছু সময় পেছানো হয়। ততক্ষণে রাত প্রায় তিনটা বেজে গেছে।
এ সময় মিশন পরিচালনা করা ব্ল্যাক টিমও অতিরিক্ত সময় পেয়ে খুশি ছিল। কারণ রকেট চালু করা ছিল পাল তোলা নৌকার দিক পরিবর্তন করার মতো দীর্ঘ প্রস্তুতির ব্যাপার। রেট্রো অফিসারের রকেটের জ্বালানি পোড়ানো শুরু করার আগে স্পেসক্রাফটের ঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে হচ্ছিল ফিডো অফিসারকে। কারণ বিস্ফোরণের কারণে স্পেসক্রাফটের গতির দিক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। গতিরও পরিবর্তন হয়েছিল।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রেডিও ও রাডার স্টেশনগুলো স্পেসক্রাফটের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য গ্রহণ করছিল। কিন্তু এগুলো থেকে স্পেসক্রাফটের সঠিক অবস্থান কিংবা দিক নির্ণয় করা যাচ্ছিল না। এগুলো থেকে প্রাপ্ত ডেটাগুলো কম্পিউটার দ্বারা বিশ্লেষণ করতে হতো। রাডার থেকে প্রাপ্ত ডেটাগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। তাই আরটিসিসির কর্মীদের খুব ঝামেলা পোহাতে হচ্ছিল। কম্পিউটার ভেক্টর নির্ণয় করতে পারছিল না। ভেক্টর দিয়ে বোঝানো হচ্ছিল মহাকাশের একটা স্থান যেখানে স্পেসক্রাফট অবস্থান করছে। যখন সেখানকার কর্মী নির্ভরযোগ্য ভেক্টর খুঁজে পেলেন, তখন ফিডোর ইলেকট্রনিক স্ক্রিনে পাঠিয়ে দেন সেটা। ভেক্টরগুলোর অনুক্রম স্পেসক্রাফটের প্রকৃত গতিপথ নির্দেশ করছিল। সেই রাতে ফিডো অফিসার অনুভব করলেন স্পেসক্রাফটের গতিপথ ভালোভাবে নির্ণয় করতে হলে তার স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় আরো বেশি ভেক্টর দরকার হবে। স্পেসক্রাফট তখন মূল গতিপথের চেয়ে অনেক দূরে বিচরণ করছিল।
যখন ফিডোর কাছে মনে হয়েছিল তিনি স্পেসক্রাফটের গতিপথ ভালোভাবে রপ্ত করতে পেরেছেন, তিনি তখন সে তথ্য তার বামে থাকা রেট্রো অফিসারের কাছে ও ডানে থাকা গাইডো’র কাছে প্রেরণ করেন। ট্রেঞ্চে থাকা তিন ডিনামিক অফিসার কন্ট্রোল রুমের সামনে থাকা চাঁদ ও পৃথিবীর রেখাচিত্র সম্বলিত বড় স্ক্রিনের এত নিকটে ছিলেন যে, তাদের কাছে মনে কখনো কখনো মনে হচ্ছিল তারাই স্পেসক্রাফট চালাচ্ছেন! পাইলটদের মতো তারাও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তারা ধুমপান করার জন্য যে দিয়াশলাই ব্যবহার করতেন, তার আবরণে ছাপার অক্ষরে লেখা ছিল ‘দ্য ট্রেঞ্চ’। অনেকটা প্রাইভেট ক্লাবের মতো। পেছনে থাকা টেলমু, ইইকম, জিএনসি প্রকৌশলীদের দলের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল অনেকটা পাইলটদের সাথে যন্ত্রের কারিগরের মতো। আর কম্পিউটার প্রকৌশলীদের সাথে সম্পর্ক ছিল বৈদ্যুতিক কারিগরের মতো।
(এরপর দেখুন পর্ব ১১ এ)